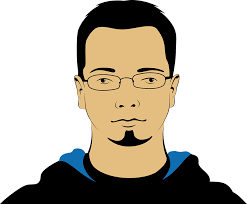


চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিনোদপুর একটি সীমান্ত এলাকা। গত কয়েক দশক আগে এই এলাকার একাধিক পরিবারের মেয়ে শিশুদের বিয়ে হয়ে ভারতে চলে যায়। সেই যাওয়াই ছিল শেষ যাওয়া। এরপর সন্তানদের সঙ্গে তাদের আর দেখা হয়নি কখনও। কারোর খোঁজ পেয়েছেন, কারোর বা খোঁজটাও পাননি। সেই গ্রামের এক মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মেয়েকে কোন ঘরে বিয়ে দিয়েছেন, পরিচয় হয়নি তাদের সঙ্গে? মেয়েকে চিঠি লেখেন। মা ঝাপসা চোখে বলেছিলেন, ‘যার কাছে বিয়ে দিসি তারেই কি ঠিকমতো চিনি’।
দেশের চারপাশে সীমান্তের কারণে এ ধরনের গল্প অনেক পাওয়া যাবে। সামাজিক সুরক্ষা দিতে পারবেন কিনা এই ভয়ে আগেভাগে বিয়ের বয়স না হতেই বিয়ে দিয়ে দেন অভিভাবকরা। আর সেই মেয়ে হয় ওপারে পাড়ি জমায়, কিংবা দেশের মধ্যেই অন্য এলাকায়। দেশের মধ্যে অন্য এলাকায় এসে প্রতারিত হয়ে বিক্রি হয়ে গেছে এমন উদাহরণও আছে। ২১ বছর বয়সী গার্মেন্টকর্মী ময়না (ছদ্মনাম) রংপুরের মেয়ে। ১৭ বছর বয়সে বাবা বিয়ে দিয়েছিল ৪৫ বছর বয়সী এক লোকের সঙ্গে। ঢাকায় বাড়ি আছে, দোকান আছে। সে ঢাকায় এসে জানতে পারে তার স্বামীর আরও এক স্ত্রী আছে, আছে দুই সন্তান। জোর করে ময়নাকে গার্মেন্টে কাজে ঢুকিয়ে বসে বসে খায় তার স্বামী। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় চলে শারীরিক নির্যাতন।
বাবা মায়ের ওপর তীব্র রাগ থেকে ময়না আর কোনোদিন যোগাযোগ রাখেনি, রংপুরে তার আর ফেরা হয়নি।
শিশুপাচার এবং বাল্যবিবাহ ক্ষতিকর অভ্যাস, যা মেয়েদের অধিকার এবং স্বাস্থ্য লঙ্ঘন করে এবং বিশ্বব্যাপী সমালোচিত, নিন্দিত হয়। উভয়ই আইন দ্বারা নিষিদ্ধ এবং উন্নয়নের ওপর তাদের প্রভাবের কারণে অনেক দেশ দ্বারা প্রধান সমস্যা হিসাবে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক আইন, রীতিনীতি এবং অনেক সংস্থার কাজ সত্ত্বেও, অনেক মেয়েশিশু, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, এখনও পাচার করা হয় বা তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়। আবার পাচার করার উদ্দেশ্যে বালিকা বিয়ে করার রেওয়াজও পুরোনো। দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাইরে মেয়েশিশু কিশোরীদের পাচার করে অনানুষ্ঠানিক নানা কাজে, এমনকি যৌনকর্মী হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বিষয়গুলো নিয়ে যে পরিমাণ কথা হওয়া দরকার ছিল এবং সতর্কতার জন্য যত রকমের প্রচারণার দরকার ছিল, তার ঘাটতি তৃণমূলে বরাবর রয়ে গেছে। এই সমস্যাগুলোর পরিমাপ নিয়ে খুব নিয়মিত কাজ হয়েছে এমনটাও নয়। পশ্চিমা গবেষকদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও নারীপাচার নিয়ে কাজ করেন এমন অনেকে বলছেন, স্থানান্তর ঘটুক বা না ঘটুক, বাল্যবিবাহ অনেক ক্ষেত্রে পাচারের সদৃশ। কেননা, এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের সঙ্গে দাসের মতো আচরণ করা হয়, কাজ করতে বাধ্য করা হয় বা যৌন সম্পর্কে লিপ্ত করা হয়, অনেকটা পাচারের শিকার শিশুদের মতোই।
বাল্যবিবাহ পাচারের মতোই বিষয়টি যেমন এখনও পুরোপুরি আলোচনায় আসেনি, ঠিক এমনকি জোরপূর্বক বিবাহকে মানবপাচার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টিও আমাদের সমাজে অনেক বেশি আলোচিত বিষয় নয়। কিন্তু এই বিষয়টিও সামাজিক পরিসরে মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে। জোরপূর্বক বিয়েকে এক ধরনের দাসত্ব হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
১৯২৫ সালের দাসত্ব কনভেনশনের ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে, দাসত্বকে ‘এমন একজন ব্যক্তির মর্যাদা বা অবস্থা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার ওপর মালিকানার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত যেকোনও বা সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়’। ১৯৫৬ সালে এসে দাসত্ব বিলোপ, দাস ব্যবসা এবং দাসত্বের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলন সম্পর্কিত সম্পূরক কনভেনশন স্বীকার করে যে বিশ্বব্যাপী দাস বাণিজ্যের অবসান ঘটানোর বিষয়টি সামনে এলেও অনেক রকম ক্ষমতা সম্পর্কে দাসত্বের অনুরূপ অনুশীলন সমাজে বিদ্যমান। জাতিসংঘ বাল্যবিবাহকে এমন একটি বিবাহ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যেখানে কমপক্ষে একজন ব্যক্তির বয়স ১৮ বছরের কম হবে। এটি আজ জোরপূর্বক বিয়ের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হিসাবে বিবেচিত হয়।
বাল্যবিবাহ হলো জোরপূর্বক বিয়েরই একটি রূপ। কারণ একটিতে সম্মতি দেওয়ার সুযোগ নেই যা একটি স্বাভাবিক, বৈধ বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয়।
আইন-কানুন ব্যাখ্যা যাই থাক না কেন। দক্ষিণ এশিয়ায় বাল্যবিবাহ কমানোর বিষয়টি কেবল প্রচারণার ওপর নির্ভর করে না। এখানে সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নারীর অবস্থান যেভাবে বিবেচিত হয় সেখানে তাকে মর্যাদাপূর্ণ জীবন দেওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকরা নানা শঙ্কায় ভোগেন। ফলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে মেয়েটির দায়িত্ব নেওয়া থেকে মুক্ত হতে চায়।
অপরদিকে, সমাজের একটা বড় অংশ এখনও নিজের দায়িত্ব নিতে পারে এমন বউয়ের চেয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া যায় এমন বউ পেতে আগ্রহী। ফলে নিষেধাজ্ঞা থাকার পরেও তারা সেটা ভাঙেন এবং কিশোরী বিয়ে করেন।
সাম্প্রতিক সময়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, নারী ও শিশু পাচারের পিছনে বাল্যবিবাহ অন্যতম কারণ। ফলে যার যার অবস্থান থেকে এগুলো রুখে দাঁড়ানো আবশ্যক। ৯ অক্টোবর ‘উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট: উইমেন্স ভয়েস অ্যান্ড লিডারশিপ বাংলাদেশ প্রকল্পের সাফল্যের গল্প’ শিরোনামে এক সম্মেলনে তিনি যখন এই কথা বলেন, তখন আরও সতর্ক হতে হয়। পাচারকে বাল্যবিয়ের সঙ্গে মিলিয়ে একটা সমন্বিত প্রতিরোধ তৈরি করা জরুরি সেটা বুঝতে সমস্যা হয় না।
আর এ পরিস্থিতি স্পষ্ট হয় নানা জাতীয় আন্তর্জাতিক জরিপের প্রতিবেদনে। বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০২৩-এ ২০০৬ থেকে ২০২২ সালের তথ্য তুলে ধরে বলা হয়েছে বয়স ১৮ হওয়ার আগেই বাংলাদেশের ৫১ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। ১৫ বছর বা তার কম বয়সী মেয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিয়ের হার ২৭ শতাংশ। এইট বিলিয়ন লাইভস, ইনফিনিট পসিবিলিটিজ শিরোনামে বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০২৩ গত ১৯ এপ্রিল বৈশ্বিকভাবে প্রকাশিত হয়।
আবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ের হার ২০০৬ সালে ৬৪ শতাংশ, ২০১২ সালে ৫২ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে ৫১ শতাংশ ছিল। তাদের হিসাবে দেশে এখন চার কোটি ১৫ লাখ মেয়ে ও নারী বিবাহিত এবং সন্তানের মা। গত ১০ বছরে বাল্যবিবাহ কমার যে হার দেখা যাচ্ছে, সে হার দ্বিগুণ হলেও ২০৩০ সালে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার হবে প্রায় ৩০ শতাংশ। যদি সেই একই ধারা অব্যাহত থাকে তবে ২০৫০ সালের মধ্যে এ হার ১৫ শতাংশের নিচে নামবে।
কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এবং বাল্যবিবাহে কেন আমাদের এই পরিমাণ আগ্রহ যাতে আইন দিয়েও ঠেকানো যায় না– এ নিয়েও বিস্তর গবেষণা চলছে।
গবেষণা বলছে, সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাবে বাল্যবিয়ে কমানো যাচ্ছে না। বরং প্রতিবছরই বাড়ছে। এরমধ্যে অভিভাবকরা সবথেকে বেশি দায়ী করেন সামাজিক নিরাপত্তার কথা। যদিও যেসব এলাকায় বাল্যবিবাহ বেশি সেসব জায়গায় কর্মরত স্থানীয় এনজিওগুলোর বিশ্লেষণ বলছে, অর্থনৈতিক কারণটাই বাবা মাকে সন্তানকে কম বয়সে বিয়ে দিয়ে পরিবার থেকে বের করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। একাধিক সন্তানের অভিভাবকরা মেয়ে সন্তানের দায়িত্ব থেকে দ্রুত অব্যাহতি চান। এর সঙ্গে আবেগের কোনও সম্পর্ক তারা দেখেন না। যার ফলে, সরকারি নানা পদক্ষেপ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগও কাজে আসছে না।
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাল্যবিবাহে বাংলাদেশ এখনও শীর্ষে। বাংলাদেশে এখন প্রতিবছর দুই শতাংশ হারে বাল্যবিবাহ কমছে। তবে এই গতিতে বাংলাদেশ থেকে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে ২১৫ বছর লেগে যাবে। তাহলে করণীয় কী। ঢাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে ইউএনএফপি’র প্রতিনিধি ক্রিস্টিন ব্লখুস একটা অভিমত জানিয়েছেন। যেখানে তিনি বলেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে বাল্যবিবাহ নির্মূলের চেষ্টা এখনকার চেয়ে ২২ গুণ বাড়াতে হবে। একদিকে কমানো, আরেকদিকে যারা ইতোমধ্যে শিকারে পরিণত হয়েছে তাদের জন্য কিছু করা। বাংলাদেশ যখন নতুন এক রাজনৈতিক বন্দোবস্তে প্রবেশ করেছে তখন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নানা বৈষম্য যেমন দূর করার পরিকল্পনা হচ্ছে, নারীর জন্য তার সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা জরুরি। যে শিশুটির পরিবার তাকে সুরক্ষা না দিতে পারার তাগিদে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে সে জানে না, তার সন্তানের ভবিষ্যৎ কী হবে।
বাল্যবিবাহের মধ্য দিয়ে স্থানান্তরের যে ভয়াবহ দৃষ্টান্ত তৈরি হয় তার না আছে কোনও সাক্ষর, না আছে তেমন জরিপ। জীবনের শুরুতেই জীবন এলোমেলো হয়ে যাওয়া এই মানুষগুলোর জন্য বেসরকারি কিছু সহায়তা উদ্যোগ থাকলেও সেগুলো কতজনইবা জানে। বেশকিছু সংগঠন পৃথক পৃথকভাবে কোনও একটি ইউনিট নিয়ে কাজ করে থাকেন। প্রকল্পকেন্দ্রিক হওয়ায় কেউ কোনও নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে জরিপ ও কেউ সাময়িক কিছু সেবা দেওয়ার কাজ করে থাকে। তবে বাল্য বিবাহকেন্দ্রিক পাচার, অভিবাসনের ফলে সহিংসতার শিকার সারভাইভার্সদের নিয়ে রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ ইউনিট (রামরু) সার্বিক কাজ করে থাকে। ফাইট স্লেভারি অ্যান্ড ট্র্যাফিকিং-ইন-পারসনস (এফএসটিআইপি) অ্যাকটিভিটি প্রকল্পে উইনরক ইন্টারন্যাশনাল বিস্তারিত কাজ করার চেষ্টা করছে যারা মনে করে, মানবপাচার বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক সমস্যার মধ্যে একটি প্রধান সমস্যা এবং এটার সঙ্গে জোরপূর্বক শ্রম, বাণিজ্যিক যৌন শোষণ, বাল্যবিবাহ জড়িত। তাদের বিবেচনায় কোভিড পরিস্থিতির পর পাচার, শোষণ এবং বাল্যবিবাহের ঝুঁকি আরও বেড়েছে। এর কারণ হিসেবে তারা জীবিকার সুযোগ কমে আসা, কর্মসংস্থানের জায়গায় নানা চ্যালেঞ্জ তৈরি হওয়াকে চিহ্নিত করে তারা। যে কারণে বাংলাদেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় সহযোগিতার জায়গায় এগিয়ে এসেছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে কাউন্সিলিং, আইনি সহায়তা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন কিনা সব একসাথে করতে পারা জরুরি। তবে তারচেয়েও খেয়াল রাখার বিষয় হলো রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল হওয়া। একজন শিশুও যেন এ ধরনের অভিজ্ঞতার শিকার না হয় সেজন্য প্রতিটি কেস কাঠামোগতভাবে অ্যাড্রেস করার কাজটি শুরু করতে হবে।
লেখক : সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী।
© All rights reserved © 2025 Coder Boss
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.